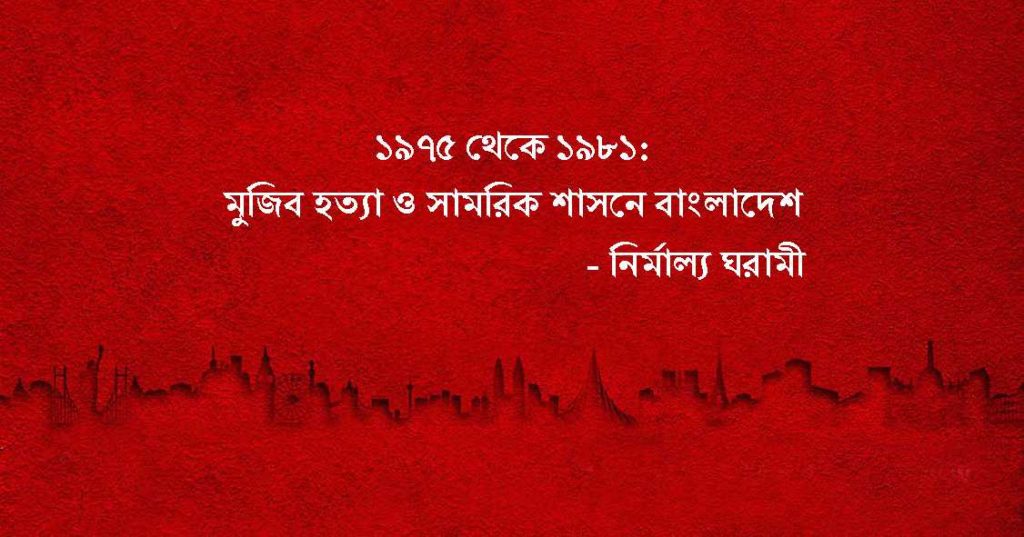
বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা পায়। সেই সময়ের ঘটনাবলী আমরা সবাই কমবেশী জানি। বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা, অব্যবহিত পর থেকেই পাক সেনা, পাকপন্থী মিলিশিয়া, আল বদর, রাজাকার, আল শামস, ইত্যাদি দ্বারা গণহত্যা আমাদের ভালই জানা আছে। কিছু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল মিলে তাদের সেই যথেচ্ছ হত্যাকাণ্ডে যে সক্রিয়/নিষ্ক্রিয় সহযোগিতা করেছিল, তাও আজ আমাদের আর অজানা নেই। অন্তত কুড়ি লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করা হয়েছিল, যদি না তিরিশ লক্ষ হয়। কু-ড়ি লক্ষ! আমরা এটাও জানি যে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কতিপয় সেনা অফিসারের নেতৃত্বে রাজধানী ঢাকায় একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই পুত্রবধূ সহ শেখ মুজিব তাঁর বাসস্থানে নিহত হন। কিন্তু এর আগের বা পরের ঘটনাগুলি আমাদের কাছে অনেকটাই অস্পষ্ট। শেষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ দেশের হাল ধরাতে পরিস্থিতি অনেকটা আয়ত্তে আসে। পরে সুযোগ বুঝে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করেন। শেষে তিনিও একসময় জনরোষের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। নির্বাচন হয় এবং বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদশের প্রধানমন্ত্রী হন।
১৯৭১ সালের ১৬-ই ডিসেম্বর বাঙলাদেশ স্বাধীন হবার সময়ে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী হয়ে ছিলেন। ইয়াহিয়ার নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। তাঁর জন্যে জেলখানায় কবরও খোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে পূর্ববঙ্গে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। পশ্চিমেও যুদ্ধ থেমে যায়। জনরোষের ভয়ে ও সার্বিক পরিস্থিতির চাপে ইয়াহিয়া ক্ষমতা ছেড়ে দেন। সেই উত্তাল পরিস্থিতিতে পাকিস্তানী জেল অধ্যক্ষের সহযোগিতায় তিনি কয়েকদিন তাঁর ঘরেই লুকিয়ে থাকেন। ইতোমধ্যে জুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্তানের ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। সেটাই স্বাভাবিক ছিল কেননা গত সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দলই পশ্চিম পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছিল। পূর্বে ফিল্ড মার্শাল আয়ুবের সামরিক শাসনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। যাই হোক ক্ষমতা পেয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে কিছু গোপন আলোচনা সেরে তিনি মুজিবকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে দিল্লীতে কয়েক ঘণ্টা থেমে মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে পা দেন। শুরু হল একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়। নেহেরুর ভাষায় বলা চলে নিয়তির সাথে অভিসার।
বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেল ঠিকই কিন্তু তার অবস্থা তখন অতি খারাপ। পাট আর চা ছিল বাংলাদেশের মূল অর্থকরী সম্পদ। কিন্তু গত এক বছরে সেই উৎপাদন প্রভূত মার খেয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ তখনও সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ পায়নি। মার্কিন মিত্র পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক বন্ধুর অভাব ছিল না- নির্জোট আন্দোলন করে নির্বন্ধু হওয়া ভারতের থেকে তার পিছনে আন্তর্জাতিক সমর্থন অনেক বেশি ছিল। পেট্রো ডলারে সমৃদ্ধ শক্তিশালী আরব দেশগুলিও ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। ফলে বাংলাদেশের রপ্তানী মার খায়। তাছাড়া এই দীর্ঘ যুদ্ধে বাংলাদেশের পরিকাঠামো-ব্রীজ, রাস্তা, সরকারী কার্যালয়, গণপরিবহণ, ইত্যাদি পুরো ভেঙে পড়েছিল। ক্রমাগত বন্যা কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। দুর্ভিক্ষের ফলে সদ্য স্বাধীন দেশটির হাল হয়ে উঠল আরও খারাপ। তাও এই সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে খাদ্যের মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল। ফলে না খেতে পেয়ে লোকে প্রচুর সংখ্যায় মারা যায়নি, কিন্তু স্বাধীন দেশে জনতার যে আশা ছিল, তা পূরণ হল না। আর মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের উচ্চাশা নাকি পূরণ হওয়ার নয়। শোনা যায় যে তাঁরা এটা চাই, সেটা দাও বলে মুজিবকে ক্রমাগত ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। তাঁদের তথাকথিত আকাশচুম্বী চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা মুজিবের ছিল না। উপরন্তু মুজিবের মন্ত্রীসভা ও আত্মীয়দের বিরুদ্ধে প্রভূত বে-আইনি কর্মকান্ডের অভিযোগ উঠল- তাঁরা নাকি সব মাত্রাছাড়া দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। কথিত এই, মুজিবের চারিদিকে একটা যে সুবিধাবাদী পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে মুজিব ব্যর্থ হলেন। কতিপয় ব্যক্তি ক্ষমতা ও সম্পদের শীর্ষে আরোহণ করলেন। দেশের লোক ক্ষুব্ধ হল।
গোদের উপরে বিষফোঁড়ার মতন মুজিব নিজের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রিক সরকার বদলিয়ে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিকেন্দ্রিক সরকারের প্রবর্তন করলেন। নিজেই হলেন রাষ্ট্রপতি। চাটুকারের দল তাঁকে ঘিরে ধরল। এখানেও না থেমে আর সব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধে ঘোষণা করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। তৈরী হল বাকশাল- বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। মুজিবের আওয়ামী লীগের সঙ্গে বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) ও জাতীয় লীগ মিলে মিশে এই নয়া দলের সৃষ্টি করল। একসময়ের জনপ্রিয় নেতা মৌলানা ভাসানী ক্রমাগত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন। তিনিও হালে পানি পাওয়ার আশায় এই ব্যবস্থাকে সমর্থন জানান। এমনকি সামরিক বাহিনীগুলি থেকেও বাকশালের সদস্য নেওয়া হল। ঠিক হল যে জেলায় জেলায় অবস্থিত আর্মির ইউনিটগুলি বাকশালের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। দলটির কার্যকলাপ অচিরেই শুরু হয়ে গেল। চারটি বাদে আর সব জাতীয় স্তরের সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ থেকে সেই একদলীয় ব্যবস্থার প্রয়োগ হবে বলে ঠিক হল। নিয়তির পরিহাস এই যে তার আগেই তিনি ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ সালে ভোরবেলায় মুজিব নিহত হলেন, আর বাকশাল কর্পূরের মতন বাতাসে মিলিয়ে গেল, অন্তত তার গর্বিত কার্যকলাপ দিশা হারাল। নেতারা মুখ লুকোলেন। লোকজন ভয়ে হোক আর ভক্তিতে হোক, তাঁর মৃত্যু নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না- অবশ্য কতিপয় কট্টর আওয়ামী লীগার বাদে। বরং জনতার একাংশ আশান্বিত চোখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ইসলামপন্থী সরকারের আগমন কামনা করল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে মুজিবের বীভৎস হত্যায় শোক করার মতন অরাজনৈতিক ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ভার হল। এমনকি একশ্রেণীর জনতা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর গ্রামের বাড়ি আক্রমণ করে তাঁর ফেলে যাওয়া সম্পদের যথাসর্বস্ব লুঠ করল!
কোন বড় ঘটনা বলে কিছু হয় না, অন্তত আচম্বিতে না। যা হয়, তা সাধারণত ছোট ছোট ঘটনার সামগ্রিক ফলাফল বা তার প্রতিক্রিয়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু নিয়েই সিন্ধু হয়ে থাকে। মুজিব হত্যা ছিল সম্ভবত সেইরকমই একটি ঘটনা- বাংলাদেশের অস্থির পটভূমিকায় বিভিন্ন সময়ে ঘটে চলা ঘটনা প্রবাহের অন্তিম ফলশ্রুতি। এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিরা বা যাঁদেরকে জড়িত হিসেবে সন্দেহ করা হয় বা যাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে এই বীভৎস ঘটনা ঘটে- তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। এবং এঁদের অনেকেই ছিলেন তাঁর কাছের লোক বা কাছের লোক হিসেবে জনসমক্ষে পরিচিত।
ঢাকা লেডিজ ক্লাবে একটা বিয়ের পার্টি হচ্ছিল। প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর শরিফুল হক ডালিম ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রী সেই পার্টি দিচ্ছিলেন। ডালিমের সম্পর্কিত বোন তহমিনার বিয়ের পার্টি ছিল সেটা। মুজিব ঘনিষ্ঠ গাজী গোলাম মোস্তাফা সপরিবারে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শোনা যায় সেই পার্টিতে গোলামের ভাই ডালিমের স্ত্রী সম্পর্কে এমন কয়েকটা কু-মন্তব্য করেন যাতে রেগে গিয়ে ডালিম তাঁকে চড়-থাপ্পড় মারেন। অচিরেই গোলামের ছেলে দলবল নিয়ে এসে মেজর ডালিম ও তাঁর স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করে। খবর চলে যায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। সেখান থেকে দ্রুত ডালিমের বন্ধু আরেক প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত মেজর নুর দলবল নিয়ে এসে ডালিমকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনা আরও এক-দু’টি কিছুটা ভিন্ন সংস্করণে প্রচলিত। তবে মূল গল্পটি মোটামুটি একইরকম। দু’দলই মুজিবসাহেবকে মীমাংসা করে দিতে বলে। কিন্তু এর ফয়সালা হল অন্যরকম। শৃঙ্খলাভঙ্গের অজুহাতে আর্মি থেকে ছাঁটাই হলেন মেজর ডালিম, মেজর নুর আর ক্যাপ্টেন হুদা। এর আগে আলাদা আলাদা কারণে (মূলত রাজনৈতিক) মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল জিয়াউদ্দিন, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল তাহের, মেজর জলিল প্রমুখ আর্মি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এইসবের ফলশ্রুতিতে আর্মির ভিতরে দেখা দিল প্রবল ক্ষোভ।
ক্ষমতা পেয়েই মুজিব মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের দুই বছরের সিনিওরিটি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ বাহিনীতে সংখ্যায় ভারী ছিলেন পাকিস্তান (পশ্চিম পাকিস্তান) থেকে ফেরা অমুক্তিযোদ্ধারা। ফলে চাপা একটা অসন্তোষ আগে থেকেই ছিল। অমুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধা-প্রত্যেকেই নিজ স্বার্থের ব্যাপারে ছিলেন চরম সংবেদনশীল। ব্যাপারটা এই নয় যে অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারেরা বাংলাদেশ বিরোধী ছিলেন। অনেকেই স্বাধীন বাংলাদেশ চান নি, এটা সত্যি। এটাও সত্যি যে অনেকেই চেষ্টা চরিত্র করেও সময়-সুযোগের অভাবে পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে পালাতে পারেন নি। বিষয়টি আরও কঠিন হয়ে গিয়েছিল এইজন্যে যে অনেকেরই পরিবার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে থেকে যাওয়া অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের অনেককেই পাকিস্তানীরা অন্তরীণ করে অসহনীয় যন্ত্রণা দিয়েছিল। ওদিকে নতুন সেনাবাহিনীতে উপরে ওঠার জন্যে শুরু হয়ে গেল ইঁদুরদৌড়। প্রত্যেকেই অন্যকে ছাড়িয়ে উপরে উঠতে চাইলেন। প্রত্যেকে চাইলেন আরও ক্ষমতা, আরও লোভনীয় পোস্টিং এবং এজন্যে তাঁরা বিবেককে পরিহার করতে অরাজি নন। আর বাংলাদেশ আর্মির মুক্তিযোদ্ধা বা অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারেরা সবাই ছিলেন আগের পাকিস্তান আমলে নিযুক্ত। পাকিস্তান পুরোনো ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুসরণ করে সেনাবাহিনীর অফিসার ক্যাডেট তৈরী করত যেখানে দেশের লোক বা সিভিল রাজনৈতিক নেতাদের উপরে তাদের বিশেষ আস্থা ছিল না, অন্তত সেই শিক্ষা-দীক্ষা তারা পেত না। ভ্রান্ত একটা সুপিরিওরিটি বোধে তারা ছিল আক্রান্ত।
১৯৭১ এর মাঝামাঝি। পূর্ব পাকিস্তান তখন ভয়ানক অশান্ত। এই পরিস্থিতিতে পাক সেনার তিন বাঙ্গালী অফিসার- মেজর মঞ্জুর (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল), মেজর আবু তাহের (পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল) ও মেজর জিয়াউদ্দিন (পরবর্তীতে কর্ণেল) পাক সীমান্ত পেরিয়ে জম্মুতে উপস্থিত হন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। একজন ভারতীয় অফিসার তাঁদেরকে ট্রেনে করে দিল্লী হয়ে কোলকাতায় নিয়ে আসার দায়িত্বে ছিলেন। তা ট্রেনে থালায় করে দু’রকম ডাল, সব্জি, পুরি দেওয়া হয়েছিল। সেই “সামান্য খাবার” দেখে মেজর মঞ্জুর ভয়ানক রেগে যান। তিনি ট্রেনের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে সেসব ফেলে দেন। বলেন যে তাঁরা সাধারণ কোন লোক নন, মিলিটারি অফিসার। তাঁদের জন্যে ভালো খাবার লাগবে, আর হ্যাঁ, সেসব আমিষ হলেই ভালো। তাছাড়া কাঁটা-চামচ ইত্যাদি দিয়ে যেন সেই খাবার যথোপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। দেশের সম্মানের জন্যে মুক্তিযুদ্ধে নাম লিখিয়েও এমন ছিল যাঁদের চিন্তাধারা, তাঁদের হাতের সামরিক বাহিনী যে সাধারণ লোকের চিন্তাধারার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, সেটা বোঝা গিয়েছিল শুরু থেকেই। সামরিক ক্যু সদ্য স্বাধীন দেশটিতে একদিন না একদিন ঘটতই। শুধু পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী তার আগমন ত্বরান্বিত করল। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে সেদিন নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরবর্তী স্টেশনে ট্রেনটি অনেকক্ষণ থামিয়ে এই তিন মেজরের জন্যে “রুচিকর” খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর তা দেওয়া হয়েছিল যতটা সম্ভব ভালো কাঁটা-চামচ-প্লেটে। এই মেজর মঞ্জুর ১৯৮১ সালের মে মাসে ছিলেন চট্টগ্রাম ক্যাণ্টনমেন্টে মেজর জেনারেল হিসেবে কর্মরত। তাঁর নেতৃত্বে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। তাঁদের ক্যু দ্রুত দমন করেন জেনারেল এরশাদ। মঞ্জুর সপরিবারে পালিয়ে যান ভারতের ত্রিপুরার দিকে। পথে তাঁদের গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। গাড়ি ফেলেই অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে চা-বাগানের এক কুলীর ঘরে আশ্রয় নেন তিনি। ভাগ্যের পরিহাসে সেদিন নিজের, স্ত্রীর বা ক্রন্দনরত সন্তানদের জন্যে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত মঞ্জুর সামান্য কিছু খাবারও জোগাড় করে উঠতে পারেন নি। কিছু পরেই পুলিশ এসে সেখান থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। সেদিনই সেনাবাহিনী তাঁকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চট্টগ্রামে ফেরে। রাতে মাথায় একটা গুলি করে তাঁকে হত্যা করে। উপরোক্ত তিনজন মেজরের মধ্যে ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে আবু তাহের হয়েছিলেন চীন ঘেঁষা সমাজবাদী আর জিয়াউদ্দিন কম্যুনিস্ট।
যা প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একমাত্র ল্যান্সার (ট্যাংক) বাহিনীর মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান ছিলেন মুজিব হত্যার মূল হোতা (যদিও পর্দার পিছনে এক বা একাধিক বিদেশী শক্তির হাত থাকলেও থাকতে পারে)। ফারুকের মামা ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অফ জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীতে তিন নম্বরে- প্রধান ছিলেন সেনাপতি তথা মুক্তিযোদ্ধা শফিউল্লাহ, দ্বিতীয় ছিলেন ডেপুটি চীফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, যিনি কালুরঘাট থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা করে অনামী এক মেজর থেকে রাতারাতি বিখ্যাত এক ব্যক্তি হয়ে যান। আর খালেদও ছিলেন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা। ফারুকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আর্টিলারির মেজর খোন্দকার আব্দুর রশিদ, যদিও রশিদ ছিলেন এক ব্যাচ জুনিয়র। তিনি ছিলেন মুজিব হত্যা পরিকল্পনায় ফারুকের মূল সহযোগী। সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন ভায়রাভাই। দুজনেই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে পাক সেনাবাহিনী ছেড়ে দেন। অবশ্য কিছু কিছু কাগজপত্রের ঘাটতি থাকায় ফারুক দুই বছরের সিনিওরিটি পাননি। তা ধরে নেওয়া হয় যে ফারুক ছিলেন মুজিব হত্যার মূল মাথা। রশিদ ছিলেন হত্যা পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার মূল হোতা। ঠাণ্ডা মাথার রশিদ জানতেন মুজিব হত্যা পরবর্তী সময়ে উপযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা না নিতে পারলে তাঁদের পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। একটা বিশাল, অভূতপূর্ব, অনিশ্চিত শূন্যতার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রয়োজনে ভারতের থেকে সামরিক সাহায্য চাইতে পারে। ফলে ক্ষমতাসীন দল থেকে কোন রাজনৈতিক নেতাকে মুজিবের উত্তরসূরী হিসেবে পাওয়া গেলে কাজটা সহজ হয়ে যাবে, বিতর্ক কম হবে। ভারতের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থাকবে না। বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র ক্যাবিনেট মিনিস্টার তথা বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ রশিদের গ্রাম সম্পর্কীয় পরিচিত ছিলেন। তিনি পূর্বে ঢাকা ও ইসলামাবাদে অ্যাডভোকেট হিসেবে বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মুজিব মন্ত্রীসভায় তুলনায় কম বিতর্কিত ব্যক্তি। রশিদ দেখা করেন মোশতাকের সঙ্গে। ক্ষমতা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন। অ্যাডভোকেট মোশতাক ধূর্ত রাজনৈতিক। তিনি ইঙ্গিত-টা লুফে নেন। এবং তাহেরুদ্দিন ঠাকুরের সহযোগীতায় ক্যু পরবর্তীতে ক্ষমতায় বসে কী ভাষণ দেওয়া যায়, তার একটা খসড়া বানিয়ে ফেলেন- সম্ভবত ফারুক বা রশিদের অজান্তেই।
বঙ্গবন্ধু মুজিব পাক শাসনে সুদীর্ঘকাল সামরিক নেতৃত্বের হাতে জেলে বন্দী ছিলেন। তিনি মোটেও সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করতে চাইছিলেন না। বস্তুত সেনাবাহিনীর থেকে তিনি বিপদের আশঙ্কা করছিলেন। উল্লেখ্য আমাদের জওহরলাল নেহেরুও সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু পরে চীনের গা-জোয়ারী মনোভাব তাঁর চোখ খুলে দেয়। অবশ্য ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে এবং তখন তাঁর শাসনের শেষদিক। যাইহোক উপরওয়ালার মতিগতি বোঝা ভার। ১৯৭৩ সালে আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে মুজিব আরব দেশগুলির প্রধান মিশরের সাহায্যার্থে অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট চা পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধের পরে কৃতজ্ঞ মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত তাঁকে তিরিশটা টি-৫৪ ট্যাঙ্ক দেন। তবে ট্যাঙ্কের গুলি-গোলা থাকত জয়দেবপুরে, সেগুলো আর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে রাখতে ভরসা পান নি। এই ট্যাঙ্ক নিয়েই ফারুক মুজিব পতনে এগিয়ে যান। যুদ্ধে ট্যাঙ্কের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব প্রচণ্ড- সাধারণ ইনফ্যান্ট্রি সেনারা ট্যাঙ্ক দেখলে দিশাহীন হয়ে যায়। কারণ ট্যাঙ্ক সব আক্রমণ হজম করে নিয়ে বিনিময়ে ভয়ানক মারণ গোলা-গুলি ছোঁড়ার ক্ষমতা রাখে, যার সামনে শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। বুলডোজারের মতন ট্যাঙ্ক-ও সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। ১৯৪৮সালে জম্মু-কাশ্মীর ফ্রন্টে পাকপন্থী আক্রমণকারীদের তাড়াতে ভারত হিমালয়ের অনেক উঁচু পাহাড়েও ট্যাংক ব্যবহার করেছিল। এবং খুব সফল হয়েছিল। তা আক্রমণের দিন ফারুকের ট্যাঙ্কে গুলি-গোলা মোটেও ছিল না। তবে সেটা কেউ জানতও না। আর ট্যাঙ্ক বাহিনীতে ফারুক দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও নিজের কাজটা খুব ভালো করে জানতেন। ফলে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন ট্যাঙ্ক বাহিনীর সর্বেসর্বা। আর ঠিক এইসময়টাতেই তাঁর ল্যান্সার বাহিনীর প্রধান কর্ণেল মোমেন কয়েকদিনের জন্যে ছুটি নেন। ফলে সেই মুহূর্তে ফারুকের হাতে ছিল সব ক্ষমতা।
মাঝে মধ্যেই রাতের দিকে রিক্সায় চেপে সাধারণ পোশাকে ঘুরতে ঘুরতে ফারুক মুজিবের বাড়ির আশেপাশে রেইকি করে আসতেন। নিজের চোখেই খুঁটিনাটি দেখতে দেখতে প্ল্যান বানাতেন। এবং পুরো ব্যাপারটি গোপন করে রাখতে সক্ষম হলেন। তা সেই ১৯৭৫ সালের ১৪ই আগস্টের কুখ্যাত রাতে মেজর ফারুক তাঁর পরিকল্পনা সবাইকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত ছিলেন ফারুক-রশিদ ছাড়াও মেজর পাশা, মেজর মহিউদ্দিন প্রমুখ এবং প্রাক্তন অফিসারেরা- ডালিম, শাহরিয়ার, রাশেদ, পাশা, নুর, হুদা। সবাই ছিলেন প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদেরকে ফারুক-রশিদ ডাক দিয়েছিলেন অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়ার জন্যে। প্রাক্তন অফিসারেরা বাজেভাবে আর্মি থেকে বাধ্যতামূলক অবসৃত, অপসারিত বা বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। একটা স্বাভাবিক প্রতিশোধস্পৃহা যে তাঁদের মনে কাজ করছিল, সেটা মিথ্যে নয়। এদিকে মেজর রশিদ ট্রাক বোঝাই সৈন্য নিয়ে তৈরী ছিলেন। আর ওদিকে ফারুক তাঁর ট্যাংক ইউনিট নিয়ে রাত্রিকালীন মহড়ায় বের হওয়ার ছুতোয় প্রস্তুত হলেন। ফারুক সবাইকে তাঁদের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিলেন। এবং মোটামুটি প্ল্যানমাফিক সব সেদিন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হল। কয়েকদিন আগেই মুজিবের প্রিয় ভাগ্নীর বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁর আত্মীয়েরা সবাই ঢাকায় ছিলেন। সুতরাং কাজে হাত দেওয়ায় সুবিধে হল। যারা মূল টার্গেট, তাদের সব এক জায়গাতেই পাওয়া যাবে। কয়েকদিন পরেই সেপ্টেম্বর থেকে বাকশাল স্থানে স্থানে আর্মি ইউনিটগুলোকেও তাদের আয়ত্তে এনে ফেলবে। তাছাড়া মুজিবের নিজস্ব রক্ষীবাহিনীর প্রধান নুরুজ্জামান তখন ছিলেন দেশের বাইরে। আর ভারত যদি হস্তক্ষেপ করে, তাহলেও সময় পাওয়া যাবে কেননা আগস্টের বর্ষাতে বাংলাদেশে অপারেশন চালাতে কালঘাম ছুটে যাবে। ফলে এটাই কাজে নেমে পড়বার প্রকৃষ্ট সময়। অপারেশন ঠিক কবে হবে সেটা এমনকি রশিদকেও অপারেশনের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে ফারুক জানিয়ে দিয়ে বাকিদের চলে আসতে নির্দেশ দেন। সবাই এলে পর ফারুক তাঁদেরকে মুজিব হত্যার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সবাই রাজি হন। শুধু পারিবারিক পরিচিতির কারণে ডালিম মুজিবের বাড়িতে অপারেশন চালাতে রাজি হলেন না।
আক্রমণের লক্ষবস্তু হিসেবে বেছে নেওয়া হল তিনটি টার্গেট- মুজিবের বাড়ি, তাঁর ভগ্নীপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবতের বাড়ি আর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণির বাড়ি। মুজিবের বাড়ির দায়িত্বে রইলেন নুর, হুদা, মহিউদ্দিন। সেরনিয়াবতের বাড়ির দায়িত্বে ডালিম। আর মণির বাড়ির দায়িত্বে থাকলেন ফারুকের আস্থাভাজন নন-কমিশনড অফিসার মোসলেউদ্দিন। মুজিবের ধানমন্ডির বাড়ির কাছে পাঁচ ট্রাক ভর্তি ১২০ জন সেনা নিয়ে নুর, হুদা, মহিউদ্দিন প্রমুখ চলে এলেন। সঙ্গে ছিল একটা হাউইটজার কামান। কামানটা বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে লাগানো হল। মুজিবের বাড়ির বাইরে পাহারায় থাকা পুলিশের লোকজনেরা সেনাদের আসতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে জায়গা ছেড়ে দিল। ভিতরে কিছু সেনা ছিল মুজিবের পাহারায়। তারাও নিজেদের লোক দেখে গেট খুলে দিল। এমন সময়ে ভিতর থেকে মুজিবের ছেলে শেখ কামালের নেতৃত্বে মুজিবের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা গুলি চালায়। ফলে দু’পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। অচিরেই কামাল মারা পড়লেন। মুজিবের ফোন পেয়ে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সদ্য নিযুক্ত ডায়রেক্টর কর্নেল জামিল ছুটে আসছিলেন। তিনি অবশ্য তখনও চার্জ হাতে পান নি। মুজিবের বাড়ির বাইরেই তাঁকে সেনারা গুলি করে হত্যা করে। এবারে ঘাতকেরা মুজিব ও তাঁর পরিবারকে খোঁজা শুরু করে দিল। আগে থেকে ঠিক ছিল যে মুজিবকে ধরে নিয়ে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে গিয়ে সংক্ষিপ্ত বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হবে বা ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হবে। কিন্তু মুজিবের ব্যক্তিত্বের সামনে পড়ে ঘাতক অফিসার মহিউদ্দিন ইতস্তত করছিলেন। তিনি মুজিবকে খুঁজে পেয়েছিলেন দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে। মুজিব মহিউদ্দিনের সঙ্গে এটা-সেটা কথাবার্তা বলে সময় কাটানোর চেষ্টা করছিলেন। এমন সময়ে প্রাক্তন মেজর নুর ছুটে এসে তাঁর স্টেনগান দিয়ে মুজিবের বুকে গুলি করেন। ওখানেই মুজিব মারা যান। একজন আগে মুজিবকে দেখেনি। সে পা দিয়ে সিঁড়িতে পড়ে থাকা তাঁর ডেড বডি উলটে দেয়। সেই অবস্থায় পরে একজন সরকারী লোক এসে তাঁর মৃতদেহের ছবি তোলে। ওদিকে মুজিবপত্নী ছিলেন কাছেই বেডরুমের দরজায়। তাঁকেও স্টেনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হল। এরপরে একে একে হত্যা করা হয় মুজিবের ছেলে আর্মি অফিসার শেখ জামাল, জামালের স্ত্রী, শেখ কামাল, কামালের স্ত্রী ও দশ বছরের ছোট্ট রাসেলকে। বেচারা রাসেল তখন আতংকে দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছিল। মুজিবের ভাই নাসের একটা বাথরুমে লুকোতে যাচ্ছিলেন। তিনিও গুলি খেয়ে মারা যান। বাসার দু’জন কাজের লোকও গুলিতে মারা যায়। মুজিবের মেয়ে শেখ রেহানা ও শেখ হাসিনা বিদেশে থাকায় তাঁরা বেঁচে যান। তবে সেদিন জামালদের সপরিবারে মারতে ঘরে গ্রেনেডও ছোঁড়া হয়েছিল বলে জানা যায়।
ওদিকে সেরনিয়াবতের বাড়ি ডালিম কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সেরনিয়াবতের ছেলে আবুল হাসনাত তাঁর স্টেনগান দিয়ে আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করেন। শেষে ম্যাগাজিন খালি হয়ে যাওয়ায় স্টেনগান সেখানেই ফেলে আত্মরক্ষার জন্যে চিলেকোঠায় উঠে যান। ঘাতকেরা ঘরে ঢুকে সেরনিয়াবতসহ আরও কয়েকজনকে হত্যা করে। তবে ভাগ্যক্রমে আবুল হাসনাত চিলেকোঠায় লুকিয়ে থাকায় বেঁচে যান। তাঁর স্ত্রী, মা, বোন সাঙ্ঘাতিক আহত হয়েছিলেন। ছোট দুই মেয়ে সোফার আড়ালে লুকিয়ে বেঁচে যায়। তাঁর ছেলেসহ অন্যান্য আত্মীয়েরা নিহত হয়। আবুল হাসনাত পরে ভারতে আশ্রয় নেন। এদিকে শেখ মণির বাড়িতে এসে মোসলেউদ্দিন মণিকে নিচে ডাকে। মণি ও তাঁর স্ত্রী নিচে এলে পর দু’জনকেই ঠান্ডা মাথায় স্টেনগানের গুলিতে মেরে ফেলা হয়। তবে আর কেউ সেখানে আক্রান্ত হয় নি।
বস্তুত মুজিবকে মারতে অন্তত ৫টি প্লট হচ্ছিল বলে প্রকাশ। কোনটা ছিল মিলিটারির, কোনটা ছিল রাজনৈতিক নেতাদের। কিন্তু কোনটাই সম্ভবত এক্ষেত্রে কার্যকর হয়নি। মুজিব কিন্তু আর্মির জুনিয়র অফিসারদের থেকে মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন না, তিনি ভয় পাচ্ছিলেন উচ্চাশা পোষণকারী সিনিয়র অফিসারদের থেকে- কিন্তু তাঁর মৃত্যু হল জুনিয়র মেজরদের হাতেই। আর ওদিকে ফারুক তাঁর ট্যাঙ্ক বাহিনী নিয়ে ঢাকা শহর চষে বেড়াচ্ছিলেন ক্যু-তে জড়িত অফিসার-সেনাদের নিরাপত্তাবিধানের জন্যে- বিরুদ্ধ শক্তির আগমন হলে তাকে রুখে দেওয়ার জন্যে। তার আর দরকার পড়ল না। মুজিব বাহিনীর কেউ কোন কাজে এল না। শুধু মুক্তিযুদ্ধের বিখ্যাত যোদ্ধা টাঙ্গাইলের “টাইগার” কাদের সিদ্দিকী ছাড়া। কিন্তু তিনিও দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্যের সামনে পড়ে পশ্চাদপসরণ করেন। পরে ভারতে আশ্রয় নেন।
যাইহোক হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই ডালিম পূর্বের প্ল্যান একটু পাল্টে নিজের উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে রেডিও-তে নিজের নামে একটা ভাষণ প্রচার করেন। সেখানে বলেন যে তাঁরা প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবকে হত্যা করেছেন। দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে। দেশ এখন থেকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে গণ্য হবে। এর প্রতিক্রিয়া ছিল সাঙ্ঘাতিক। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এক চরম অনিশ্চিত দশা। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, সেনাবাহিনী সিনিয়র অফিসারেরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক এই পরিস্থিতির ফায়দা উঠিয়ে দেশে নতুন শাসকের আগমন ত্বরান্বিত করল ক্যু সৃষ্টিকারী মেজরেরা।
খোন্দকার মোশতাককে রশিদ তাঁর বাসা থেকে একরকম জোর করেই তুলে আনলেন। অবশ্য আসতে আসতে তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে মেজরেরা তাঁকে সত্যি সত্যিই প্রেসিডেন্ট বানাতে চান, গুলি করে মেরে ফেলার ইচ্ছে তাঁদের নেই। তিনি ধূর্ত মানুষ, হাই কোর্ট-সুপ্রীম কোর্টের এক সফল আইনজীবী। বহু পদস্থ লোককে চরিয়েছেন। তাঁকে যখন বলা হল প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাষণ দিতে, তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দিলেন যে আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্স- এই তিন বাহিনীর প্রধান তাঁর নামে আনুগত্য না নিলে তিনি দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নন। ফলে মেজরেরা গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজনকে প্রায় ধরেই নিয়ে এল। তিনজনেই তখন হতচকিত। পরবর্তী খবরে প্রকাশ মেজর জেনারেল জিয়া, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্ণেল শাফায়াত জামিলের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সহযোগিতায় এত অল্প আয়াসে তাঁদেরকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। আর্মি, নেভী ও এয়ারফোর্সের প্রধান মোশতাকের পক্ষে আনুগত্যের শপথ নেন। এবারে মোশতাক আগে থেকেই তাহেরুদ্দিন ঠাকুরের সহযোগিতায় বানিয়ে রাখা শপথবাক্যটি পাঠ করেন। তবে তিনি দেশটির রাজনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন এনে দেশটিকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র করতে চাইলেন না। শুধুমাত্র বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। শোনা যায় দেশটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত না হওয়ায় লন্ডনের প্রতিপত্তিশালী সিলেটিরা (লন্ডনের ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁগুলির মালিক মূলত তারাই) বা বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক লোক অসন্তুষ্ট হয়। সৌদি রাজা ফয়জল-ও এই সিদ্ধান্তে অখুশি ছিলেন। পরবর্তীতে এরশাদ এই “ভুল”-টি শুধরে নেন। তবে তাঁর আগে প্রেসিডেন্ট জিয়া মহান আল্লাহের কাছে বাংলাদেশকে উৎসর্গ করেন। যাইহোক পরে মোশতাক আসেন বঙ্গভবনে- প্রেসিডেন্টের বাসস্থানে এবং মেজরেরা সেখানেই অধিষ্ঠিত হন। মৌলানা ভাসানীও নিমেষে দলবদল করে এবারে মোশতাককে সমর্থন দেন। তা মেজরদের তত্ত্বাবধানে বঙ্গভবন থেকেই একের পর এক অর্ডার বেরোতে থাকে। দ্য ইন্ডেমনিটি অর্ডিন্যান্স-১৯৭৫ জারি করে ক্যু-তে জড়িত সবাইকে তাঁদের অপরাধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিছুদিনে মধ্যেই সেনাবাহিনীর প্রধান শফিউল্লাহকে সরিয়ে দিয়ে জিয়াকে করা হয় আর্মির সেনাপ্রধান আর প্রমোশন দিয়ে তাঁর ডেপুটি করা হয় এরশাদকে। সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিমানবাহিনীর প্রধান এ কে খোন্দকারের জায়গায় জার্মানী থেকে তোয়াবকে উড়িয়ে এনে তাঁকে এয়ারফোর্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এটা করেন সেই মেজরেরাই।
মুজিবের মৃত্যুতে কারা কারা লাভবান হন? এই তালিকা শেষ হবে না। তবে প্রাথমিকভাবে প্রেসিডেন্ট খোন্দকার, তাহেরুদ্দিন ঠাকুর সহ ক্যাবিনেট মিনিস্টারেরা যথোপযুক্ত মর্যাদা পান। বিশেষ করে খোন্দকার মোশতাক প্রভূত লাভবান হন। জিয়া হন আর্মির প্রধান। সুতরাং তিনিও লাভবান হন। কিন্তু বুদ্ধিমান মোশতাক জিয়ার উপরে রেখে দেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান রিটায়ার্ড কর্ণেল ওসমানীকে এবং আর্মি-নেভী-এয়ারফোর্সের চীফ অফ ডিফেন্স স্টাফ হিসেবে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে। আর জিয়ার সঙ্গে জুড়ে দেন এরশাদকে। অভাবনীয়ভাবে চার মাসে ডবল প্রমোশন পেয়ে যান এরশাদ, যিনি কিনা আর্মির রেগুলার অফিসার ছিলেন না। এরশাদ কোহাতের অফিসার ট্রেনিং স্কুল থেকে পাস করেছিলেন, মিলিটারি অ্যাকাডেমী থেকে নয়। আর মেজর রশিদ, ফারুক প্রমোশন পেয়ে হন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল। ডালিম, নুর, হুদা প্রমুখ আবার আর্মিতে ফিরে এলেন। ডালিম, নুর প্রমুখ প্রাক্তন মেজরদের সার্ভিসের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল হিসেবে প্রমোশন দেওয়া হল, প্রাক্তন ক্যাপ্টেন হুদা হলেন মেজর। বিমানবাহিনীর প্রধান হন তোয়াব। সুতরাং উপরোক্ত ব্যক্তিদের অনেকেই যে মুজিব হত্যা ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকবেন, তাতে আর সন্দেহ কী?
মেজরেরা ছাড়া আর কারা কারা মুজিব হত্যায় জড়িত ছিলেন, তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপরে বিচার করে আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে। প্রথমত জিয়াকে যখন মেজর রশিদ মুজিব হত্যার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে নিরুৎসাহ করেন নি। শুধু বলেছিলেন যে তিনি সিনিয়র আর্মি অফিসার হিসেবে এইসবে জড়িত হতে চান না। তবে মেজরেরা চাইলে তারা এগিয়ে যেতেই পারে। শুধু তাই না মুজিব হত্যার কিছুদিন আগে থেকে প্রাক্তন মেজর নুর বা ডালিম যখন আর্মি ক্যান্টনমেন্টে টেনিস খেলার অছিলায় আসতেন, সেটারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন জিয়া। তিনিই শফিউল্লাহকে সরিয়ে হয়েছিলেন আর্মি চিফ। ফলে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তাঁর একটা অদৃশ্য প্রভাব ছিলই। রশিদকে যখন যশোরে বদলি করা হয়েছিল, তখন সেটা আটকে দিতে সক্রিয় হয়েছিলেন রশিদের উপরওয়ালা কর্ণেল শাফায়াত জামিল এবং আর্মির চীফ অফ জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। তাছাড়া মুজিব হত্যার দিন সংবাদ পেয়েও মোশাররফ বা শাফায়াত সারাদিন বেশ হাশি-খুশি মেজাজে ছিলেন, শফিউল্লাহের ডাকে সাড়া দেন নি। শাফায়াতের অধীনে ছিল ৪০০০ সৈন্যের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিগেড অর্থাৎ তিনি কারুর সম্মতি ছাড়াও প্রয়োজনে নিজে থেকেই অ্যাকশনে নেমে যেতে পারতেন, বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি মুজিবের বাড়ি আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ শফিউল্লাহের কাছ থেকে শোনার পরে। সেটা তিনি করেন নি। শফিউল্লাহ ফোন করে মুজিবের বাড়িতে ট্রুপ পাঠাতে বললেও তিনি এড়িয়ে যান। পরে তিনি বাসার টেলিফোন নাকি উঠিয়ে রাখেন যাতে তাঁকে ফোনে না ধরা যায়। কিছু পরে বরং ধীরে সুস্থে হেঁটে হেঁটে গিয়ে তিনি জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অভিযোগ এই যে তাঁর তো তখন উচিত ছিল গাড়ি নিয়ে তৎক্ষণাৎ শফিউল্লাহের কাছে ছুটে আসা। এবং ট্রুপ রেডি করতে হুকুম দেওয়া। তাছাড়া তাঁর বাসার পিছন দিয়েই ট্যাঙ্কগুলো সেদিন রাতে বিকট শব্দে মুভ করেছিল। পরে রশিদ দাবি করেছিলেন যে শাফায়াত সব জানতেন। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ খালেদ মোশাররফকে পাঠিয়েছিলেন শাফায়াত তাঁর ট্রুপ মুভ করতে দেরী করছেন কেন, সেটা দেখতে, পারলে তাড়াতাড়ি ফোর্স মুভ করতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি শাফায়াত জামিলের সঙ্গে মিলে গিয়ে খবর পাঠালেন যে শাফায়াত তাঁর কথা শুনছেন না, তাঁকে কিছু করতেও দিচ্ছেন না। ওদিকে খালেদ মোশাররফ মুজিব হত্যার কিছু পরে ট্যাঙ্কগুলিকে গুলি-গোলা সরবরাহ করার হুকুম জারি করেন। ফলে ট্যাঙ্কগুলি এবারে সত্যি সত্যি চলমান দুর্গে পরিণত হয়। তাছাড়া তিনি মুজিব হত্যার সংবাদ শুনেও ক্যান্টনমেন্টে উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা করেন নি। ফলে ডালিম এসে একরকম জোর করেই সেনাপ্রধান শফিউল্লাহকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যান মোশতাকের পক্ষে শপথ নেওয়ার জন্যে। অথচ শাফায়াত জামিল বা খালেদ মোশাররফ ছিলেন মুজিবের বিশেষ প্রিয় ব্যক্তি। সম্ভবত ক্ষমতার লোভ, খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা বিবেক-বুদ্ধি সবকিছুকে পরাস্ত করে। তবে মুজিব হত্যা পরবর্তী সময়ে খালেদ বা শাফায়াত কোন প্রমোশন পান নি। এর ফলে তেসরা নভেম্বর, ১৯৭৫ তাঁরা নিজেরাই অভ্যুত্থান করেন।
আশ্চর্যের বিষয় এই যে পূর্বোক্ত গাজী গোলাম মোস্তাফা বা তাঁর পরিবারের কেউ এই ক্যু-তে আক্রান্ত হন নি। ফলে এটা আন্দাজ করা যেতেই পারে যে ডালিম বৃহত্তর চক্রান্তে যুক্ত ছিলেন না, ছিলেন দাবার ঘুঁটি মাত্র। মাথা গরম এই প্রাক্তন আর্মি অফিসারকে হয়তো শুধুই ব্যবহার করা হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ডে। কে বা কারা পিছন থেকে সমগ্র পরিকল্পনায় জড়িত আর্মি অফিসারদের পুতুলের ন্যায় নাচাচ্ছিলেন, সেটা আজও অজানা। অনুরূপে “পাপা কর্ণেল” রূপে পরিচিত স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সামরিক প্রধান কর্নেল ওসমানী একটি অতীব গোপনীয় মিটিং-এ অংশ নিয়েছিলেন যেখানে জিয়া ছাড়াও মেজর রশিদ ও মেজর ফারুক ছিলেন। ফলে ওসমানীর সম্পৃক্ততাও অনুমান করা যায়। তাছাড়া মুজিব হত্যার পরে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক।
খোন্দকার মোশতাক ছিলেন ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগরের বিদেশ মন্ত্রী। খবরে প্রকাশ যে তাঁর সঙ্গে কিছু পশ্চিমা বিদেশী শক্তি যোগাযোগ করেছিল যাতে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি ছেড়ে দিয়ে দলত্যাগ করে পাকপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলান। এই খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে পর তাঁর মন্ত্রিত্ব চলে যায়। এর শোধ তিনি সুদে আসলে এবং নৃশংসভাবে পরে তুলেছিলেন মুজিবনগর সরকারের চার প্রাক্তন স্তম্ভ- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন আহমেদ, কামরুজ্জামান, মনসুর আলিকে কারাগারে হত্যা করে। সেই মোশতাকই হয়েছিলেন মুজিব হত্যা পরবর্তী সরকারের প্রধান। আবার ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে বাঙালী সামরিক অফিসারেরা আটকা পড়েন। অনেককেই অন্তরীণ করা হয় বা বন্দী করা হয়। এরশাদও এইসময়ে পাকিস্তানে ছিলেন। অভিযোগ এই যে পরবর্তী সময়ে ১৯৭১-৭৪ এর মধ্যে বারে বারে তিনি পাকিস্তান থেকে তাঁর ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র বিশেষ প্লেনে করে নিয়ে এসেছিলেন যখন পাকিস্তান আর বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় ছিলই না। অর্থাৎ পাকিস্তানে তাঁর হয়তো বিশেষ শক্তিশালী এক বা একাধিক কনট্যাক্ট ছিল। তিনিই হয়েছিলেন মুজিব হত্যা পরবর্তী সময়ে আর্মির ডেপুটি চীফ- জিয়ার পরেই। চার মাসে তিনি একরকম নিয়মবিরুদ্ধভাবে দু’টি প্রমোশন পান, খালেদ মোশাররফকে সরিয়ে হয়ে যান জিয়ার ডেপুটি।
মুজিবের মৃত্যু কি ঠেকানো যেত? এখানে অনেক ব্যাপার জড়িয়ে আছে। আমাদের পক্ষে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে সংকীর্ণ। কিছু একটা হতে চলেছে এই আঁচ পেয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর প্রধান ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে নিজেই বাংলাদেশে আসেন। তিনি মুজিবকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাজ হয় নি। ক্যু-এর সময়ে মেজর মহিউদ্দিন যখন মুজিবকে খুঁজে পান, তখন মুজিব তাঁর সঙ্গে কথা বলে ঘরের ভিতরে গিয়ে ফোন করে আর্মি প্রধান শফিউল্লাহের থেকে সাহায্য চাইলেন। ওদিকে ভগ্নীপতি সেরানিয়াবতও ফোন করে মুজিবের থেকে সাহায্য চাইলেন। যাইহোক সামরিক সাহায্য আর আসেনি। কেন? ঢাকায় প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা তথা বর্তমান কর্ণেল শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিগেড ছিল। এবং রশিদ তাঁর অধীনেই ছিল। ঘটনার পরে রশিদ এসে তাঁকেই রিপোর্ট করেন। অভিযোগ যে মুজিবকে হত্যার কথা শুনে রশিদকে তিনি গ্রেপ্তার করতে পারতেন, সেটা করেন নি। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ ফোন করে তাঁর থেকে সাহায্য চাইলেও তিনি চুপ করে ছিলেন। বরং তিনি গিয়ে ডেপুটি চিফ জিয়া’র (জিয়াউর রহমান) সঙ্গে দেখা করেন। কেন? পরে অবশ্য তাঁর আত্মজীবনীতে বা এই ঘটনার পরে তিনি ক্যু সৃষ্টিকারী এইসব আর্মি অফিসারদের সম্পর্কে অনেক কটু কথা বলেছিলেন। পরবর্তীতে মেজরদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে, তাদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে আনার জন্যে শাফায়াত পরবর্তী সেনাপ্রধান জিয়াকে বারে বারে অনুরোধ করেন। যাইহোক অজ্ঞাত কোন কারণে ক্যু-এর দিনে তিনি নীরবতা দেখিয়েছিলেন। মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের প্রধান রউফ ছিলে অ-মুক্তিযোদ্ধা অফিসার। তাঁর উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে মুজিব তাঁকে সরিয়ে কর্ণেল জামিল আহমেদকে তাঁর পদে আসীন করার অর্ডার বের করেন, যদিও সেটা কোন কারণে তখনও অবধি কার্যকর হয়নি। দেরী হল কেন? খালেদ মোশাররফ হয়তো বলতে পারতেন। মুজিবের ফোন পেয়ে কর্ণেল জামিল ছুটে যান মুজিবের বাসায়, কিন্তু সেখানেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তা রউফ সাহেব ভোর ৩টের মধ্যেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে ক্যু হতে চলেছে, মুজিবের বাসায় হামলার ২.৩০ ঘণ্টা আগেই। কিন্তু তিনি কাউকে সেটা জানান নি। কথিত আছে উল্টে বৌ-বাচ্চা নিয়ে রাতের পোশাকেই গলফ খেলার মাঠের মধ্যে ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় তিনি আত্মগোপন করেন। মুজিব হত্যার পরে ভোরে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসেন। তাঁর আচরণ ছিল রহস্যে ঢাকা। তিনি সময়ে খবরটা পাঠিয়ে দিলে পর মুজিব নিশ্চিত বেঁচে যেতেন। আর সেদিন মুজিবের বাসাতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার ও নিচের দরজা ছিল খোলা। কামাল সেই দরজা দিয়ে নিচে নেমে স্টেনগান হাতে ক্যু’র মোকাবিলা করেন। সেই দরজাদু’টি লাগানো থাকলেও এত সহজে মুজিবের নাগাল পেত না হত্যাকারীরা। সেদিন ভাগ্য বারে বারে মুজিব ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে গেছে। সম্ভবত শফিউল্লাহ আর এক-দু’জন ব্যক্তি বাদে বাকি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে খুব কম জনই সেদিন ছিলেন নিষ্পাপ। এবং এঁরা প্রায় সবাই ছিলেন প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঘটনা এই যে মুজিব ভেবে রেখেছিলেন সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ-এর মেয়াদ তিন বছরের জন্যে বাড়িয়ে দেবেন। গোপনে খবরটা পেয়ে জিয়া হয়তো হাত কামড়ান, খালেদ-ও হতাশ হন। তাঁদের পক্ষে আর মুজিবকে পছন্দ করার সঙ্গত কোন কারণ থাকল না।
সামনাসামনি দেখলে ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের সেনা অভ্যুত্থান ছিল প্রকৃতপক্ষে কতিপয় মেজরদের অভ্যুত্থান। অন্যেরা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকলেও সরাসরি অপারেশনে নামেন নি। ভাবটা এই যে মেজরেরা শত্রু নিপাত করলে পর আমরা ফাঁকা গোলে কিক নেব। পরিকল্পনার চরম গোপনীয়তা, কয়েকজন উপরওয়ালা আর্মি অফিসারের সক্রিয়/নিষ্ক্রিয় সহযোগিতা এবং নিম্নপদস্থ অফিসার হিসেবে রাডারের বাইরে থাকা- মূলত এই ক’টি কারণে অপারেশনটি সফল হয়। বস্তুত কোন একটি জায়গাতে বাধা পেলেই অপারেশনটি সেদিন ভেস্তে যেত। কিন্তু অপারেশন সফল হওয়ায় মেজরদের আর পায় কে? সেদিন সবকিছুই তাঁদের পরিকল্পনামাফিক চলেছিল। উল্টে ডালিমের রেডিওতে দেওয়া ভাষণের ফলে সাধারণ জনগণের উপরে সাঙ্ঘাতিক রকমের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়েছিল। সবাই হয়ে গিয়েছিল নিশ্চুপ। মেজরেরা এটা ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে মুজিবের জনপ্রিয়তা এখন তলানিতে। একবার তাঁর মৃত্যু সংবাদ সবাই জেনে গেলে কেউ আর বিশেষ ট্যাঁ-ফোঁ করবে না। তা-ই হল। মেজরেরা এবারে প্রমোশন পেয়ে বঙ্গভবনে জাঁকিয়ে বসলেন। বুদ্ধিমান খোন্দকার মোশতাক মেজরদের ম্যানেজ করে বেশ ভালই দেশ চালাতে থাকলেন।
সমস্যাটা হল শাফায়াত জামিল ও খালেদের। শাফায়াতের অধীনস্থ রশিদ হিরো হয়ে বঙ্গভবনে জাঁকিয়ে বসলেও শাফায়াত প্রমোশন পেলেন না। অথচ তিনি যদি তাঁর ট্রুপ সেদিন মুভ করাতেন, তাহলে এই মেজরেরা আজ কোথায় থাকতেন? সব ঝুলতেন ফাঁসিতে। খালেদ দেখলেন যে পরোক্ষভাবে সহায়তা দিলেও তাঁর হাল হল আগের চেয়েও বাজে। মুজিব বেঁচে থাকলে আজ নয় কাল জিয়াকে সরিয়েই দিতেন। সেবারে জিয়াকে সরিয়ে বিদেশে একটা কূটনৈতিক পোস্টিং দিতে চাইলেও বুদ্ধিমান জিয়া সেটা কোনগতিকে কাটিয়ে দেন। তবে তা ছিল সাময়িক। আর জিয়া সরে গেলেই খালেদ হতেন আর্মির চীফ, কেননা শফিউল্লাহ একদিন না একদিন সরেই যেতেন। উল্টে জিয়ার অধীনে খালেদ কাজ করছেন, আর একরকম ডাবল প্রমোশন পেয়ে “নন-রেগুলার” অফিসার এরশাদ হয়ে গেছেন তাঁর বস- জিয়ার ঠিক নিচেই এখন এরশাদের অবস্থান। তাছাড়া এই মেজরেরা ক্যু করে এটা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন যে সফল হলে পর ক্ষমতার ফোয়ারা উন্মোচিত হবে তাঁদের সামনে, তাঁদের সব অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে। তাঁরাই হয়ে উঠবেন দেশের মুখ। ক্ষমতার এই মোহ সাঙ্ঘাতিক। যে সব প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার আগে প্রচুর ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে পাক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দেশের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁরাই এবারে ক্ষমতার মোহে একের পর এক বিপথে পা বাড়াতে থাকলেন। ক্যু-এর পর ক্যু-তে আমজনতা বিভ্রান্ত তথা অভ্যস্ত হয়ে উঠল। আমরা শুধু মুজিব হত্যা পরবর্তী কয়েকটি অতীব গুরুত্বুপূর্ণ ক্যু নিয়ে অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।
খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিল মিলে ৩ নভেম্বর, ১৯৭৫ সালে সেনাপ্রধান জিয়াকে বন্দী করে পাল্টা ক্যু করলেন। কিন্তু ক্যু পরবর্তী বিষয়ে আগে থেকে তাঁরা ঠিকমতন ভেবে রাখেন নি। এটাই তাঁদের জন্যে চরম ক্ষতিকর প্রমাণিত হল। মাত্র আড়াই মাসে দেশের জনগণ মোটেও মোশতাকের উপরে বিরূপ হয়ে যায়নি। জিয়ার উপরেও সাধারণ সেনাদের ধারণা খারাপ ছিল না। বস্তুত জিয়া একজন ক্ষমতালোভী ধূর্ত ব্যক্তি হলেও অন্যদিকে তিনি ছিলেন খুব সৎ অফিসার। সাধারণ সেনাদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। যখন তাঁকে গৃহবন্দী করে বলা হল যে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হবে, তিনি প্রথমেই একজনকে বললেন ঢাকা শহরে তিনশ টাকায় ভালো একটা বাড়ি দেখে দেওয়ার জন্যে। সেই অফিসার তাঁকে জানালেন যে ন’শ টাকার কমে ভাল বাড়ি কোন জায়গাতেই পাওয়া যাবে না। শুনে জিয়া খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। তা ক্যু করেই শাফায়াত আর খালেদ নিজেদের প্রমোশন, আর এটা-সেটা কাজে যখন সময় অপব্যয় করছিলেন, তখন তলে তলে পূর্বে উল্লেখ্য মোসলেউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি দল ঢাকাতে কারাগারে গিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন আহমেদ, কামরুজ্জামান, মনসুর আলিকে গুলি করে-বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঘটনাটি ঘটেছিল ফারুক-রশিদের পূর্বের প্ল্যানমাফিক যাতে নতুন ক্যু-এর ফলে দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন আওয়ামী লীগ নেতা বেঁচে না থাকেন। বিষয়টি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট মোশতাক শুধু যে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন, তা নয়, তিনি এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন। ইতোমধ্যে নব্য ক্যু নেতাদের সঙ্গে পূর্বের ক্ষমতাসীনদের একটা চুক্তি হয়। ফলে মোশতাক প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেন। আর পূর্বের অভ্যুত্থানের মেজরেরা তাঁদের সঙ্গীসাথী, স্ত্রী-বান্ধবীদের নিয়ে ব্যাংককের প্লেনে নিরাপদে চেপে বসেন। অনেকে বলেন যে এই ক্যু ছিল প্রথম ক্যু-এর সরাসরি বিপরীত। সেটা পুরোটা ঠিক নয়। কেননা এই ক্যু-এর নেতারা- শাফায়াত জামিল বা খালেদ কারাগারে বন্দী আওয়ামী লীগ নেতাদের মুক্তির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না। তাঁরা তখন তাঁদের কেরিয়ারের কথাই ভাবছিলেন। আসলে খালেদের মা, ভাই ছিলেন আওয়ামী লীগার। ফলে লোকের মনে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যে এই নয়া ক্যু আগের ক্যু-এর বিরুদ্ধে, আর এতে ভারতীয়দের মদত রয়েছে। ক্যু করার সময়ে রটে গিয়েছিল যে ভারতের চর হিসেবে খালেদ কাজ করছেন। আর বাংলাদেশে ভারতপন্থীর চেয়ে বড় অভিশাপ বা দুর্নাম হয় নাকি? যাইহোক ঘটনাপ্রবাহ ইঙ্গিত করে না যে খালেদ-শাফায়াত ভারতের পক্ষে কাজ করছিলেন। তাহলে এতটা কাঁচা প্ল্যান নিয়ে তাঁরা মাঠে নামতেন না। অনেকের মতে জিয়া নিজেই এই ক্যু ঘটিয়েছিলেন। তাঁর ইঙ্গিতেই তাঁকে শাফায়াত গৃহবন্দী করে নিজের ব্রিগেডের লোক দিয়ে ঘিরে রাখেন, কিন্তু প্রাণে মারেন নি। আগে থেকেই শাফায়াতের সঙ্গে জিয়ার সুসম্পর্ক ছিল। জিয়া দেখছিলেন যে তিনি সেনাবাহিনীর চীফ হয়েছেন বটে, কিন্তু মাথার উপরে ওসমানী, খলিলুর। প্রেসিডেন্ট মোশতাক নিজে থেকে জিয়ার সঙ্গে কথাই বলেন না। তাহলে আর ক্ষমতা কোথায়?
ধূর্ত জিয়া তলে তলে চীনপন্থী রিটায়ার্ড কর্ণেল (প্রকৃতপক্ষে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল) আবু তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। তাহের জাসদ-এর (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) সদস্য ছিলেন। জাসদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুজিবের একসময়ের অনুগামী মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল আলম খান। জাসদের মিলিটারি উইং-এর প্রধান ছিলেন তাহের। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তাঁকে আর্মি থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেখলেন যে এই সুযোগ। সাধারণ সেনাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে তলে তলে সাধারণ সেনাদের মধ্যে তাঁদের মতাদর্শ অনুপ্রবেশ করাতে তাহের সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে জিয়ার সাহায্যে দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করা সম্ভব। সাধারণ সেনাদের অনেক ন্যায্য-অন্যায্য ক্ষোভকে পুঁজি করে জাসদ তাদের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। এবারে জিয়ার পক্ষে তারা মাঠে নামল। খালেদ-শাফায়াতের বিরুদ্ধে সাধারণ সেনাদের উসকে দিয়ে (বিশেষ করে খালেদ ভারতপন্থী ও ভারতের চর এই প্রচার চালিয়ে) জিয়াকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা হল। সেনারা তখন শ্লোগান দিচ্ছিল- সেপাই সেপাই ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই। ৬ নভেম্বর মাঝরাতে অর্থাৎ কাগজে কলমে ৭ তারিখে ঘটল এই ঘটনা। পালটা ক্যু-এর খবর পেয়ে খালেদ-শাফায়াত পালালেন। খালেদ আশ্রয় নিলেন ১০ ইস্ট বেঙ্গলে। এই বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অধীনে কাজ করেছিল। ভেবেছিলেন যে এবারে তারা তাঁকে খালি হাতে ফেরাবে না। হায়রে ভাগ্য! এরাই বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে হত্যা করে ডেড বডি সম্ভবত বেয়নেট দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে। পরে জিয়ার কাছে সেই বডি নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে আরও দু’জন আর্মির অফিসার নিহত হন। শাফায়াত জামিল বঙ্গভবনের পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনি প্রাণে বেঁচে যান। পরে তাঁকে আর্মি থেকে ছাঁটাই করা হয়। ক্ষমতার অলিন্দে এবার জিয়া ও তাহের।
তাহের ভেবেছিলেন যে জিয়াকে সামনে রেখে সেনাবাহিনীর সাহায্যে দেশটির নিয়ন্ত্রণ হাতে নেবেন। ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীর সাধারণ সেনারা অফিসারদের হেনস্তা, হত্যা করতে মেতে উঠেছে। তাহের ছিলেন কট্টর ভারতবিরোধী এবং চীনপন্থী কিন্তু জিয়া ছিলেন বাস্তববাদী, রক্ষণশীল এবং পাশ্চাত্যমুখী। ফলে তেলে জলে মিশ হল না। তাহের সাধারণ সেনাদের পক্ষে ব্যাটম্যান প্রথা বাতিল সহ অনেক শর্ত দিলেন যেমন সেনাদের মধ্যে থেকেই অফিসার নিয়োগ করতে হবে, উন্নত বাসাবাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে, অধিক বেতন দিতে হবে, এইসব। বলাবাহুল্য কয়েকটি ছাড়া বাকিগুলি মেনে নেওয়া সম্ভব না। এই পরিস্থিতিতে তাহেরের সঙ্গে জিয়ার ঝামেলা শুরু হল। কতিপয় মাত্র সেনা জিয়ার পক্ষে থাকল। আর অফিসারেরা। বাদবাকি সব সেনা বিদ্রোহী হল। অবশ্য অফিসারদের লাঞ্ছনা তখন শুরু হয়ে গেছে। কেউ মারা গেলেন, কেউ বোরখা পরে, পাঁচিল টপকে বা অন্যভাবে পালিয়ে গেলেন, কারুর সাম্মানিক ব্যাজ কেড়ে নেওয়া হল, কোন কোন অফিসার রক্তাক্ত দেহে ক্যান্টনমেণ্টে পড়ে থাকলেন। অনেক ছোটাছুটি করে, সেপাইদের বাবা-বাছা করে, সেপাইদের মধ্যে থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কতিপয় নন-কমিশনড অফিসারদের নিজ পক্ষে এনে, নাটুকেপনার সাহায্যে জিয়া সেই পরিস্থিতি কোনরকমে সামলে দেন। তাহের বন্দী হন। বিচারে ফাঁসি হয়। ২১শে জুলাই, ১৯৭৬ সালে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।
মুজিব হত্যায় মূলত প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধারাই যুক্ত ছিলেন। পাক আর্মি ছেড়ে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া অফিসারদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হয়ে উঠেছিল যে তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাপ্য মর্যাদা পান নি। এঁরাই ছিলেন আর্মিতে প্রথম সারিতে। অ-মুক্তিযোদ্ধা অফিসারেরা প্রথমদিকে কিছুটা নিষ্প্রভ ছিলেন। ফলে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ব্যালান্স করার জন্যে জিয়া অন্য অফিসারদের তুলে আনতে শুরু করলেন। এভাবেই অ-মুক্তিযোদ্ধা অফিসারেরা সামনের সারিতে এগিয়ে এলেন। তাছাড়া সেনাবাহিনীতে অ-মুক্তিযোদ্ধা অফিসারেরাই ছিলেন সংখ্যায় ভারী। ফলে নতুন কাউকে তুলে আনলে অ-মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের উঠে আসার সম্ভাবনা ছিল বেশি। তাই জিয়ার শাসনে অ-মুক্তিযোদ্ধা অফিসারেরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিগ্রহণ করেছিলেন।
পূর্বের মুজিবঘাতক মেজরদেরকে বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক পোস্টে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। ফারুক, রশিদ, ডালিম, পাশা- এঁরা জিয়াকে উৎখাত করার জন্যে একের পর এক পরিকল্পনা করেই গেলেন। কিন্তু কোনটিই ফলপ্রসূ হল না। উল্টে একবার ফারুক, ডালিম, রশিদ প্রমুখ পৃথকভাবে ঢাকায় ফিরেছিলেন ক্যু ঘটানোর জন্যে ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে। কিন্তু জিয়াও চোখ-কান খোলা রেখেছিলেন। তিনি জোর করে ডালিম-রশিদকে ফের ব্যাঙ্ককের প্লেনে তুলে দেন। ফারুক একাই বগুড়াতে ল্যান্সার ইউনিটে পৌঁছে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বলা বাহুল্য সেই ক্যু সফল হয়নি। প্ল্যানিং-এর কিছুই ছিল না এই ক্যু-তে। ফারুক প্রথমে গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে ছাড়া পেলে পর ফারুককেও প্লেনে করে লিবিয়ায় পাঠিয়ে দেন জিয়া। ফারুক, ডালিম, রশিদকে কূটনৈতিক পদ দিয়ে জিয়া সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন। ফারুক-রশিদ রাজি হন নি। তবে ডালিম রাজি হয়েছিলেন। এঁদের কোন ক্ষতি না হলেও বিদ্রোহী সাধারণ সেনানীদের কাউকে কাউকে ফাঁসিতে চড়তে হয়, অনেককে জেলে পচতে হয়। কেউ কেউ হয় চাকুরিচ্যুত।
জিয়া ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেন। ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ মিশরীয় গোয়েন্দা সূত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর পেয়ে যায়। আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর জিয়াকে বিমান বাহিনী দিবসে মেরে ফেলা হবে। একটি বামপন্থী দলের গুপ্ত সদস্যেরা বিমানবাহিনীর কতিপয় এয়ারম্যানের সঙ্গে মিলে এই কাণ্ডটি ঘটাবে। এদিকে জিয়া এই খবর পান ২৫শে সেপ্টেম্বর যখন তিনি কায়রোতে মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাতের সঙ্গে বসে মিটিং করছিলেন। কোন ইউনিট জিয়াকে হত্যা করতে চাইছে, সেটা অবশ্য সাদাত সঠিক বলতে পারেন নি। এদিকে জিয়ার দেশে ফেরার কথা ২৭শে সেপ্টেম্বর। জিয়া পড়লেন দোটানায়। অবশ্য শেষ অবধি বিমান বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানটি হয়নি কেননা জাপানী কম্যুনিস্টরা জাপান এয়ারলাইন্সের একটি প্লেন হাইজ্যাক করে ঢাকায় অবতরণ করায়। সেটা তখন বোম্বে থেকে রওনা দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে রফা করার জন্যে এয়ারফোর্সের প্রধান নিজেই কন্ট্রোল টাওয়ারে চলে আসেন। ফলে ২৮শে সেপ্টেম্বর সেই অনুষ্ঠান আর হয়নি। এদিকে বিদ্রোহের দিন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। ফলে বিমানবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠান না হওয়ায় বিদ্রোহীরা আর অপেক্ষা করতে রাজি হল না। বগুড়া, ঢাকা, যশোরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। ঢাকায় বিদ্রোহী সেনাদের সঙ্গে যোগ দিল কুর্মিটোলা এয়ারবেসের কয়েকশ’ বিদ্রোহী এয়ারম্যান। এটা ছিল একধরনের সিপাহী বিদ্রোহ। আগের সিপাহী বিদ্রোহে জিয়া ছিলেন নায়ক। সিপাহীরা জিয়াকে খালদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিলের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে এনেছিল। আর এখানে সিপাহীরা জিয়ার মুন্ডু চাইল। তবে গভীর জলের মাছ হিসেবে খ্যাত জিয়াও ছিলেন প্রস্তুত। জিয়া দ্রুত পরিস্থিতি আয়ত্তে নিয়ে আসেন। শেষে ১১৪৩ জনকে ফাঁসিতে চড়ান। কয়েকশ’ বিদ্রোহীকে দশ বছর অবধি শাস্তি দেন। অনেককেই ছাঁটাই করা হয়। এবং অভিযোগ এই যে কোর্ট মার্শালের ন্যূনতম পদ্ধতিও জিয়া মেনে চলেন নি। এইভাবে নারকীয়তার সঙ্গে বদলা নেন জিয়া। তবে এত করেও বিদ্রোহের বীজমুক্ত হল না বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী।
পূর্বে বর্ণিত মেজরেরা আবার বিদ্রোহ করার জন্যে মুখিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয়বারের ব্যর্থ বিদ্রোহ তাঁদের “নাম-যশ”-কে “কালিমালিপ্ত” করেছিল। তাঁরা তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় মিলিত হয়ে আবারও বিদ্রোহের নীল নকশা বানাতে থাকলেন। এবারে ঠিক হল যে তাহেরের রেখে যাওয়া জাসদ ও সেনাবাহিনীর জওয়ানদের হতাশাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৮০ সালের জুন মাসে বিদ্রোহ করতে হবে। জিয়া যথাসময়ে সব খবর পেয়েও গেলেন। এবং এই বিদ্রোহ-ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। মুজিব হত্যায় যুক্ত মেজর পাশা লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পদ পেয়েছিলেন। তিনিও ফারুকদের সঙ্গেই বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। তিনি তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় কূটনৈতিক পদে ছিলেন। বিদ্রোহের অন্যতম হোতা পাশা বাংলাদেশে এসেছিলেন ক্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। শেষে বন্দী হয়ে তিনি রাজসাক্ষী হন। এবং বেঁচে যান। এছাড়াও অসংখ্য ছোট-খাট বিদ্রোহ হয়েছিল। জিয়া সহজেই সেসব দমন করেন। বিদ্রোহী অফিসারদের ক্ষমা করলেও সাধারণ সেনাদের প্রতি তিনি কঠিন ব্যবস্থা নেন।
শুধু ১৯৮১ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ জিয়া দমন করতে পারলেন না। একসময়ের সহযোগী মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে থাকলেন। তাঁকে বদলি করলেন চট্টগ্রামে। ১৯৮১ সালের ২৯শে মে জিয়া তাঁর দলের (বি এন পি) কাজে চট্টগ্রামে আসেন। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের গোয়েন্দারা তাঁকে চট্টগ্রামে যেতে নিষেধ করেছিল। নিদেনপক্ষে বলেছিল যেন তিনি সেখানে রাত না কাটান। জিয়া শুনলেন না। তিনি রাতে থাকলেন চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে। সেখানেই মূলত চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের অফিসারেরা বিদ্রোহ করে তাঁকে বন্দী করে। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মতিউর রহমান গুলি চালিয়ে জিয়াকে হত্যা করেন যদিও মঞ্জুর চেয়েছিলেন জিয়াকে বন্দী করতে। জিয়া হত্যা চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ সেনারা ভালোভাবে নেয়নি। তারা শুরুতে বিদ্রোহী অফিসারদের পক্ষ নিলেও ধীরে ধীরে দলে দলে তাঁদের ছেড়ে ঢাকাস্থিত এরশাদের দলে যোগ দিতে থাকে। সুযোগসন্ধানী এরশাদ ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীর সর্বেসর্বা হয়ে গিয়েছিলেন, কেননা আগেই বলেছি তিনি ছিলেন জিয়ার ডেপুটি। দ্রুত হাতে বিদ্রোহ দমন করেন এরশাদ। মঞ্জুর পালাবার সময়ে একজন চা শ্রমিকের কুটীরে ধরা পড়েন। চট্টগ্রামে ফিরিয়ে এনে তাঁকে হত্যা করা হয়। অনেকেই বলাবলি করেন যে অন্তরালে থেকে এরশাদই কলকাঠি নেড়েছিলেন। তিনিই জিয়া হত্যাকারী মতিউরের সঙ্গে সিনিওরিটি ভেঙে একাধিক গুপ্ত মিটিং করেন। তাঁর প্ররোচনাতেই মতিউর জিয়াকে হত্যা করেন। ওদিকে বিদ্রোহী মতিউর অভ্যুত্থান বিরোধী সেনাদের হাতে মারা যান। এবারে একচেটিয়া ক্ষমতা পেয়ে গেলেন এরশাদ। কিছুদিন পরে প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান করে তিনি নিজেই বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হলেন।
মুজিব হত্যার চক্রান্তকারীদের কয়েকজন পরে শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় ফাঁসিতে ঝোলেন। কয়েকজন এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ফারুক, হুদা, মহিউদ্দিন, শাহরিয়ার- এঁদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। ক্যাপ্টেন মাজেদকে ভারত সরকার নাকি গোপনে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করায়। তিনিও ফাঁসিতে ঝুলেছেন। মোসলেউদ্দিনকেও এপ্রিল, ২০২০তে ভারত সরকার নাকি বাংলাদেশের হাতে তুলে দিয়েছে। ডালিম সম্ভবত পাকিস্তানে লুকিয়ে আছেন। নুর হয়তো আছেন কানাডায়। সম্ভবত রশিদ ও রাশেদ আছেন আমেরিকায়। পাশা জিম্বাবোয়েতে মারা গেছেন বলে শোনা যায় যদিও সেই সংবাদ সত্যি নাও হতে পারে। তবে এটা বলা যায় যে অপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া আজও শেষ হয়নি।
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অস্থিরতা আমাদের পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশ তার সামরিক একনায়কতন্ত্রের যুগ থেকে দীর্ঘদিন হল বেরিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধিতেই ভারতের মঙ্গল। উপরোক্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আর্থিক ক্ষেত্রে কল্পনাতীত দ্রুত উন্নতি করে চলেছে। বনধ, ঘেরাও, চাক্কা জ্যাম, অবরোধ- এইসব সংস্কৃতি সেখানে নেই। ফলে শিল্পক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হচ্ছে না, হবে না এইসব শ্লোগানের পরিবর্তে তাঁদের প্রথম পছন্দ করতে হবে, এবং তা এখনই। আমাদের ন্যায় অন্ধ পশ্চিমা বিরোধীতা তাঁরা করেন না (তবে আমেরিকান ভিসা পেলে আমরাও সব “ন্যায়-নীতি” পরিহার করতে রাজি)। ফলশ্রুতিতে বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, ফুড প্রসেসিং, ওষুধশিল্পে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক, অনেক এগিয়ে গেছেন। চা-পাট শিল্পেও এগিয়ে। ভারী শিল্পেও তাঁরা দ্রুত এগিয়ে আসছেন। বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি করে চলেছে এবং প্রতিবেশি হিসেবে তার উন্নতিতে আমাদেরই মঙ্গল।
তথ্যসূত্রঃ
১। বাংলাদেশঃ রক্তের ঋণ- অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস (হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা)
২। তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা- লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এম এ হামিদ (শিখা প্রকাশনী, ঢাকা)
৩। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর- কর্ণেল শাফায়াত জামিল (অবঃ)[মফিদুল হোক, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা]
৪। জাসদের উত্থান-পতনঃ অস্থির সময়ের রাজনীতি- মহিউদ্দিন আহমদ (প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা)
৫। রহস্যময় অভ্যুত্থান ও গণফাঁসি- জায়েদুল আহসান (চর্চা প্রকাশক, ঢাকা)
৬। পূর্বাপর ১৯৭১ পাকিস্তানী সেনা গহ্বর থেকে দেখা- মেজর জেনারেল মহম্মদ খলিলুর রহমান (অবঃ) [সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা]
৭। ইন্টারনেট
 utoldhara.com সপরিবার বাঙলির মনের ঠিকানা
utoldhara.com সপরিবার বাঙলির মনের ঠিকানা






